
তৃণমূলের স্বাস্থ্য নিরাপত্তাঃ
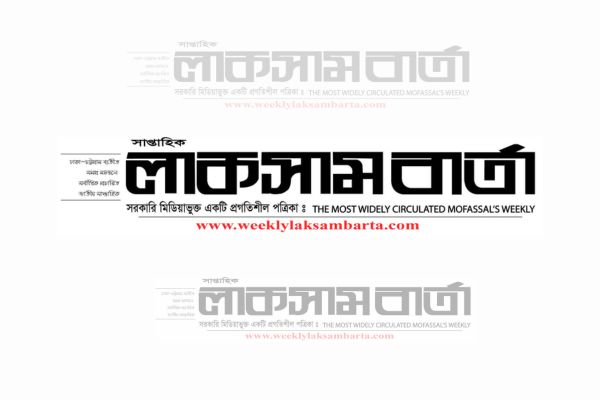
তারিক সাইদ হারুন\ একটি দেশের সত্যিকারের অগ্রগতি নির্ভর করে তার জনগণের সুস্থতার ওপর, শুধু ইট-পাথরের উন্নয়নে নয়। বাংলাদেশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতিও লাভ করেছে। বাংলাদেশে মোট চাহিদার ৯৫ শতাংশ ওষুধ সাশ্রয়ী মূল্যে দেশেই উৎপাদিত হয়। এমনকি ক্যানসারের মতো রোগের ওষুধও কম দামে দেশে পাওয়া যায় এবং এর সব ধাপের ওষুধ এখন দেশেই উৎপাদিত হয়। যেমন-প্যানক্রিয়াটিক ক্যানসারের কেমোথেরাপির জন্য ব্যাংককে যেখানে ৬ লাখ টাকা লাগে, বাংলাদেশে সেই একই সেবা মাত্র ৬০ হাজার টাকায় পাওয়া যায়।
তবে, স্বাস্থ্য খাতে বেশকিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। যদিও মানসম্মত মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া নাগরিকের অধিকার, বাংলাদেশের জনগণ তা সঠিকভাবে পাচ্ছে না। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির ১ শতাংশেরও কম বরাদ্দ দেয়া হয়, যা দুঃখজনক। স্বাস্থ্য খাতের অনেক বড় বড় ভবন অব্যবহৃত পড়ে আছে। কোথাও অবকাঠামো থাকলেও ডাক্তার নেই, আবার কোথাও ডাক্তার থাকলেও নার্স নেই। প্রতি ১০ হাজার মানুষের জন্য মাত্র ৫.২৬ জন চিকিৎসক এবং ২.২২ জন নার্স রয়েছে, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদন্ডের চেয়ে অনেক কম। এছাড়া, মাত্র ৫১ শতাংশ মানুষ প্রয়োজনের সময় মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পায়, অর্থাৎ প্রায় ৪৯ শতাংশ মানুষ এ সেবার বাইরে রয়ে গেছে। দেশের ৬২ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করলেও ৭৫ শতাংশ চিকিৎসক সেবা দেন শহরাঞ্চলে।
স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়নের মডেল
বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়নের দু’টি প্রধান মডেল প্রচলিত আছে। একটি হলো ‘বেভারিজ মডেল’, যা সাধারণ করভিত্তিক অর্থায়ন। ১৯৪৮ সালে উইলিয়াম বেভারিজের হাত ধরে ব্রিটেনে এর সূচনা হয়। আরেকটি হলো ‘বিসমার্ক মডেল’, যা স্বাস্থ্যবিমাভিত্তিক। জার্মানির সাবেক চ্যান্সেলর অটো ভন বিসমার্কের নামে ১৮৮৩ সালে জার্মানিতে সামাজিক স্বাস্থ্যবিমার মাধ্যমে এ মডেলের শুরু হয়। বাংলাদেশের সরকারি স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়ন করভিত্তিক হওয়ায়, এটি বেভারিজ মডেলের কিছু বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। তবে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে অর্থায়নের মডেলটি কেমন হওয়া উচিত, তা নীতিনির্ধারকদের কাছে এখনো স্পষ্ট নয়। সরকারি অর্থায়ন শক্তিশালী করা হবে নাকি সামাজিক স্বাস্থ্যবিমা চালু করা হবে, এ বিষয়ে কোনো সুরাহা হয়নি।
স্বাস্থ্যসেবার পেছনে রোগীর ব্যক্তিগত খরচ অনেক বেশি। এ ছাড়া প্রতি বছর প্রায় ৭ লাখ মানুষ চিকিৎসার জন্য বিদেশে যায় এবং এর পেছনে প্রায় ৩৫০ কোটি ডলার ব্যয় করে। এটি দেশের স্বাস্থ্যসেবার ওপর মানুষের আস্থার অভাবকেই তুলে ধরে।
এনজিও এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও সক্ষমতা
প্রায় ১৮ কোটি মানুষের দেশে সরকারের একার পক্ষে স্বাস্থ্যসেবার উন্নতি করা সম্ভব নয়। দেশের মোট স্বাস্থ্যসেবার প্রায় ৭০ শতাংশ বেসরকারি সংস্থা, হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং মেডিকেল কলেজের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তৃণমূলে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে এনজিওগুলো সরকারের সহায়ক শক্তি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । স্বাধীন বাংলাদেশে গত ৫০ বছর ধরে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। যেমন-গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, কুমুদিনী ট্রাস্ট, ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন এবং ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন উল্লেখযোগ্য।
এনজিওগুলো সরকারের পুষ্টি কর্মসূচি, এইচআইভি/এইডস ও য²া নির্মূল কর্মসূচিতে সহযোগিতা করছে। ব্র্যাকের কর্মীরা খাবার স্যালাইন তৈরির কৌশল শিখিয়েছেন এবং এনজিওগুলো স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল বিতরণে সহায়তা করেছে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে এবং প্রশিক্ষিত ধাত্রী তৈরিতেও এনজিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া, যে কোনো দুর্যোগে তারা খাবার পানি, ওষুধ ও জরুরি পুষ্টিসামগ্রী নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ায়। করোনা মহামারির সময়ও এনজিও-কর্মীরা মানুষকে সচেতন করা, আক্রান্তদের চিহ্নিত করা এবং নমুনা পরীক্ষায় সহায়তা করাসহ বিভিন্ন কাজে যুক্ত ছিল।
ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। শুধু মাইক্রোক্রেডিট অথরিটির সনদপ্রাপ্ত এনজিওর সংখ্যাই ৭২৪টি। প্রায় ২৫ হাজার শাখার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানগুলো ৪ কোটি ১৫ লাখ দরিদ্র পরিবারকে ঋণ ও অন্য সেবা দিচ্ছে। প্রতি পরিবারে যদি ৪ জন সদস্য থাকে, তাহলে প্রায় ১৬ কোটি ৬০ লাখ মানুষ এ কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮৪ শতাংশ। এ এনজিওগুলোর ২.৫ লাখ প্রশিক্ষিত কর্মী বাহিনী রয়েছে, যারা প্রতিদিন দেশের প্রতিটি গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।
সমন্বিত অংশীদারত্বের জন্য সুপারিশ
বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতকে শক্তিশালী করতে সরকারের বিদ্যমান অবকাঠামোর সঙ্গে এনজিও এবং ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের মাঠপর্যায়ের বিস্তৃত নেটওয়ার্ককে কৌশলগতভাবে যুক্ত করা অপরিহার্য। এ সমন্বয়ের জন্য একটি শক্তিশালী অংশীদারত্ব গড়ে তোলা জরুরি।
এর জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি ‘ন্যাশনাল এনজিও হেলথ কোলাবোরেশন প্ল্যাটফর্ম’ গঠন করা যেতে পারে, যা এনজিওগুলোর স্বাস্থ্যসেবা-সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহ ও বিতরণে কাজ করবে। ক্ষুদ্রঋণভিত্তিক এনজিওগুলোর প্রতিদিনের সমিতি সভায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা সেশন চালু করা হলে প্রায় ৮৪ শতাংশ মানুষের কাছে নিয়মিত স্বাস্থ্যবার্তা পৌঁছানো সম্ভব হবে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এবং পিকেএসএফের মাধ্যমে এনজিওগুলোর জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ডাইজড হেলথ মডিউল চালু করলে মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করা যাবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উচ্চ ব্যক্তিগত খরচ কমাতে নির্বাচিত এলাকায় পাইলট সামাজিক স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প চালু করে মডেল তৈরি করা যেতে পারে। এনজিওগুলোর সংগৃহীত স্বাস্থ্য তথ্যকে জাতীয় ডেটাবেসে যুক্ত করে নীতিনির্ধারণে ব্যবহার করলে প্রকৃত সেবার প্রভাব নিরূপণ সহজ হবে।
এ সমন্বিত পদ্ধতি সরকারি নীতি, এনজিওর মাঠপর্যায়ের সক্ষমতা এবং আর্থিক সুরাকে একীভূত করে তৃণমূলে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে। লেখকঃ উন্নয়ন কর্মী
সম্পাদক ও প্রকাশক:
শহীদুল্লাহ ভূঁইয়া
সহযোগী সম্পাদক: তোফায়েল আহমেদ
অফিস: সম্পাদক কর্তৃক আজমিরী প্রেস, নিউমার্কেট চান্দিনা প্লাজা, কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত ও ১৩০৭, ব্যাংক রোড, লাকসাম, কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত। ফোন: ০২৩৩৪৪০৭৩৮১, মোবাইল: ০১৭১৫-৬৮১১৪৮, সম্পাদক, সরাসরি: ০১৭১২-২১৬২০২, Email: laksambarta@live.com, s.bhouian@live.com