সম্পাদকীয় বাড়াতে হবে তরুণদের কর্মসংস্থান
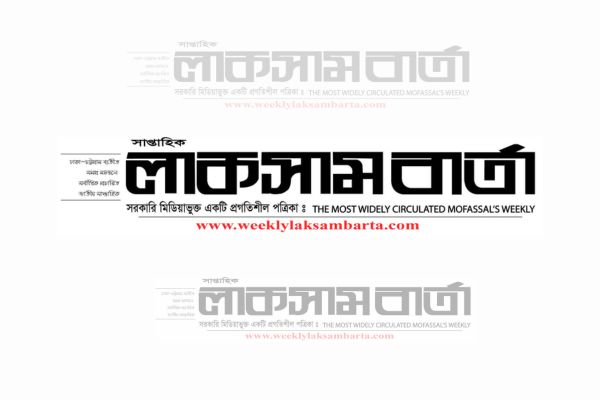
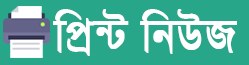
বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিস্থিতি নিয়ে সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা তথা রাজনৈতিক স্থিরতার অভাবে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে প্রবৃদ্ধিতে ব্যাপক ভাটা দ্রশ্যমান। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ৪ ধরনের চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো- বেসরকারি বিনিয়োগে শ্লথগতি, কর্মসংস্থানে স্থবিরতা, ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাংক খাত ও রাজস্ব আদায়ে ক্রমাবনতি। শুধু বিশ্ব ব্যাংক নয়; দেশের অর্থনীতিবিদরাও সরকারকে অর্থনীতি ঠিক পথে পরিচালিত করতে, বিভিন্ন খাতে সংস্কারের পাশাপাশি দ্রæততম সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কাটানোর তাগিদ দিয়ে আসছেন। এ কথা সত্য যে, ২০২৪-এর ৫ই আগস্টের পর থেকে নাগরিকদের একটা বড় উদ্বেগের কারণ দেশের ভঙ্গুর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। গত প্রায় ১৫ মাসেও পুলিশ তার স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরতে পারেনি। মব-সহিংসতা, চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, চাঁদাবাজি, মুক্তিপণের মতো অপরাধ আশঙ্কাজনকভাবে বাড়লেও এসব অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এই বিষয়গুলো বেসরকারি বিনিয়োগে সরাসরি প্রভাব পড়ছে। ফলে বাড়ছে না কর্মসংস্থান গতি। বরং প্রতিদিনই কর্ম হারাচ্ছে মানুষ।
বিশ্বব্যাংক বলছে, বাংলাদেশে এক বছরের ব্যবধানে দারিদ্র্য বেড়েছে। শ্রমশক্তিতে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের হার কমেছে। তারা আরও বলছে, ৩০ লাখ কর্মক্ষম নারী-পুরুষ শ্রমশক্তির বাইরে চলে গেছেন, যার ২৪ লাখই নারী। এ পরিসংখ্যান অত্যন্ত উদ্বেগজনক। নারীর ক্ষমতায়নে যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো দরকার, সেখানে এই উল্টোযাত্রা ভাবিয়ে তোলার মতো। দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্যের সংখ্যা যে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে, সেটা বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন পিপিআরসির সাম্প্রতিক গবেষণাতেও উঠে এসেছে। সংস্থাটির প্রতিবেদন জানাচ্ছে, দেশে এখন দারিদ্র্যের হার ২৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ।
নেতিবাচক এই পরিসংখ্যানগুলো বলছে, দেশে বেকারের সংখ্যা দ্রæত বাড়ছে। চাকরির বাজার সংকুচিত হয়ে পড়ায় ভোগান্তির মুখে শিক্ষিত বেকাররাও। অথচ জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছিল চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক কড়া প্রতিবাদ। গত প্রায় ১৫ মাসে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি বললেই চলে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী যুব বেকারদের মধ্যে প্রায় ২৯ শতাংশ স্নাতক। দেশে এক বছরের ব্যবধানে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে ১ লাখ ৬০ হাজার। ২০২৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বেকারের সংখ্যা ছিল ২৬ লাখ ২০ হাজার, যা ২০২৩ সালে ছিল ২৪ লাখ ৬০ হাজার। অন্য যে কোনো বিভাগের তুলনায় চাকরির খোঁজে ঢাকাতেই অবস্থান করেন বেশিরভাগ বেকার। যাদের অনেকেই আবার উচ্চশিক্ষিত। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, দেশের শ্রমবাজারে নিরক্ষর শ্রমিকের সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লাখ।
পরিসংখ্যান বলছে, দেশে কাজে নিয়োজিতদের ৮৪ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে। গ্রামে এ হার ৮৭ দশমিক ৫৮ শতাংশ, শহরে ৭৩ দশমিক ৭৬ শতাংশ। নিরক্ষর কর্মশক্তি দেশের অর্থনীতির উৎপাদনশীলতায় তৈরি করছে সীমাবদ্ধতা। বিশেষ করে শিল্প ও সেবা খাতে দক্ষতা ঘাটতির কারণে অনেকে কাজ পেলেও উচিত মূল্য পাচ্ছেন না। কর্মসংস্থানের কাঠামোতেও বড় বৈষম্য ধরা পড়েছে। বিপুল শ্রমশক্তি এখনো সুরক্ষাহীন, সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত। শিক্ষিত বেকারের হার বেপরোয়াভাবে বৃদ্ধির প্রবণতা সমাজে হতাশা সৃষ্টি করছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যও তা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষিত বেকারদের এক ক্ষুদ্র অংশ বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করলেও অন্য অংশ হতাশায় দিন কাটাচ্ছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপে দেশে বেকারের যে তথ্যচিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, লাখ লাখ বেকারের এই দেশে দক্ষ জনশক্তির অভাবও প্রকট। দেশের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে শিক্ষিত বেকার সৃষ্টির বদলে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে ব্যবহৃত হয়, সে উদ্দেশে সরকারকে এখনই সক্রিয় হতে হবে।
পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী দেশে বর্তমানে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ সরাসরি বেকার, তবে অনানুষ্ঠানিক ও আংশিক বেকারদের অন্তর্ভুক্ত করলে এ সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ছাড়িয়ে যায়। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর এক বড় অংশ কোনো না কোনোভাবে অপ্রতুল কাজে নিয়োজিত- অর্থাৎ তারা কাজ করছে, কিন্তু তাদের আয় জীবিকা নির্বাহের জন্য যথেষ্ট নয়। শহরের তুলনায় গ্রামীণ অঞ্চলে আংশিক বেকারত্ব বেশি। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে ধীরে ধীরে শিল্প ও সেবা খাতে রূপান্তর ঘটলেও সেই হারে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়নি। জানা যায়, প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ নতুন তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে, কিন্তু নতুন চাকরি তৈরি হচ্ছে সর্বোচ্চ ৭-৮ লাখ। বাকিরা হয় বেকার থেকে যাচ্ছে, নয়তো অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে অনিশ্চিত কাজে নিযুক্ত হচ্ছে। এতে দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ-তরুণ জনগোষ্ঠী আজ ক্রমে হতাশ হয়ে পড়ছে।
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও শ্রমবাজারের চাহিদার মধ্যে বড় ধরনের অমিল রয়েছে। অধিকাংশ উচ্চশিক্ষা এখনো তাত্তি¡ক। যেখানে বাস্তব প্রশিক্ষণ বা দক্ষতা অর্জনের সুযোগ খুবই সীমিত। দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই বাণিজ্য, সমাজবিজ্ঞান ও মানবিক বিষয়ে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। কিন্তু এ খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। অন্যদিকে শিল্প, কৃষি, প্রযুক্তি ও কারিগরি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের চাহিদা থাকলেও প্রশিক্ষিত কর্মী পাওয়া যাচ্ছে না। কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর না দিলে এই সমস্যা আরও গভীর হবে। উন্নত দেশগুলোয় শিক্ষার সঙ্গে শিল্প ও উদ্যোক্তা সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটানো হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও সেই উদ্যোগ দেখা যায় না। নানা সময়ে সরকার কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণে কিছু প্রকল্প নিয়েছে। কিন্তু সেগুলোর গতি খুবই ধীর।
দেশের অর্থনীতি মূলত শ্রমনির্ভর হলেও শিল্পায়নের গতি আশানুরূপ নয়। গার্মেন্টস খাতই এখনো কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় উৎস, কিন্তু এ খাতেও সম্প্রতি অর্ডার কমে যাওয়ায় নতুন নিয়োগের হার কমেছে। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাত, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের বড় চালিকা শক্তি হতে পারত, সেটি নানা প্রতিবন্ধকতায় জর্জরিত। ব্যাংকগুলো বড় করপোরেট ঋণে মনোযোগ দিচ্ছে। ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় মূলধন পাচ্ছেন না। দেশে এখনো বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ পুরোপুরি তৈরি হয়নি। জটিল প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, দুর্নীতি, বিদ্যুৎ সংকট ও নীতিগত অনিশ্চয়তা বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করছে। নতুন শিল্প স্থাপন কমে যাওয়ায় চাকরির সুযোগও সীমিত হয়ে পড়েছে। বরং দেশে বেশ কয়েকটি পোশাক শিল্প কারখানা বন্ধ হওয়ার খবর গণমাধ্যমে এসেছে।
বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৮-১০ লাখ শ্রমিক বিদেশে যায়। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেই হার কমেছে। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ অভ্যন্তরীণ শ্রমনীতি পরিবর্তন করেছে। আবার ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ার শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা বেড়েছে। বিদেশে এখন অদক্ষ নয়, বরং দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বেশি। অথচ বাংলাদেশ থেকে পাঠানো শ্রমিকদের একটি বড় অংশ অদক্ষ। ফলে সুযোগ থাকা সত্তে¡ও অনেক বাজার আমরা হারাচ্ছি। বিদেশে যেতে আগ্রহী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে সরকার ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রযুক্তিগত ও ভাষাগত প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করলে রেমিট্যান্স আয় আরও বাড়ানো সম্ভব হবে এবং অভ্যন্তরীণ বেকারত্ব কিছুটা হলেও কমবে।
সর্বোপরি বেকারত্ব কেবল আমাদের অর্থনৈতিক সংকটই নয়; এটি এক ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি। কর্মহীন তরুণ সমাজের একাংশ ক্রমে হতাশা, মাদকাসক্তি ও অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। দেশে কিশোর গ্যাং, চাঁদাবাজি, অনলাইন প্রতারণা ও সহিংসতার ঘটনাগুলো আংশিকভাবে এই বেকারত্বের ফল। একজন বেকার যুবক শুধু নিজের পরিবারকেই নয়, গোটা সমাজকেও অস্থিরতার মধ্যে ফেলে দেয়। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি বেকারত্ব পারিবারিক সম্পর্কে চাপ সৃষ্টি করে। মানসিক রোগের ঝুঁকি বাড়ায় এবং সামাজিক বৈষম্যকে গভীর করে তোলে। একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জন্য এই পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক।
ভুলে গেলে চলবে না, তরুণ সমাজ আগামী বাংলাদেশের চালিকাশক্তি। তাদের যদি আমরা অবহেলা করি, তবে উন্নয়ন টেকসই হবে না। এখনই সময় শিক্ষা, শিল্প ও বিনিয়োগ নীতিকে পুনর্বিন্যাস করার। বেকারত্ব রোধে স্বল্পমেয়াদি ভাতা বা সহায়তা নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দরকার- যেখানে শিক্ষা, প্রযুক্তি, শিল্প ও উদ্যোক্তা খাত একে অপরের পরিপূরক হবে। সরকার, বেসরকারি খাত ও নাগরিক সমাজ- সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। বেকারত্বের মেঘ কেটে গেলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আবারও নতুন সূর্যোদয় দেখবে। অন্যথায় উন্নয়নের অর্জনগুলো ভেসে যাবে অনিশ্চয়তার ¯্রােতে। আর আমরা হারাব আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি-তরুণ মানবসম্পদ। তাই তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ বাড়াতে হবে। অর্থনীতি পুনর্গঠন, শিক্ষা সংস্কার ও প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি ‘কর্মক্ষম জাতি’ হিসেবে বিশ্বে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করতে পারবে।

